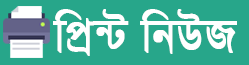
ঢাকা মিরপুরের বাসিন্দা আব্দুল মালেককে প্রতি মাসে তার বাবা-মার উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের জন্য ওষুধ কিনতে হয়। এছাড়াও তিনি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম কিনে থাকেন। তিন মাস আগে এসব ওষুধ কিনতে তার মাসে প্রায় ৬ হাজার টাকা খরচ হতো। কিন্তু এখন একই পরিমাণ ওষুধ কিনতে তাকে ৮ হাজারের বেশি টাকা গুনতে হচ্ছে। শুধু মালেক নন, তার মতো অসংখ্য মানুষ ওষুধের দাম বৃদ্ধির কারণে বাড়তি খরচ বহন করছেন, যদিও তাদের আয় একটাকাও বাড়েনি। সরকারি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে বছরে ৮৬ লাখের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে।
দেশে দেড় হাজারেরও বেশি জরুরি ওষুধের ২৭ হাজারেরও বেশি ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন হয়। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ২১৯টি ওষুধ রয়েছে, যার মধ্যে ১১৭টি ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সরকার নির্ধারণ করে দেয়। বাকি ওষুধের মূল্য কোম্পানিগুলো নিজেরাই নির্ধারণ করে। সংশ্লিষ্টদের মতে, ওষুধের দাম নির্ধারণে সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কাঁচামাল, লেবেল, মোড়ক সামগ্রী, মার্কেটিং খরচ এবং ডলারের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে কোম্পানিগুলো ওষুধ প্রশাসনকে ম্যানেজ করে বা ভুল বুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে।
বাজারে বিভিন্ন ফার্মেসি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, একমি কোম্পানির মোনাস ১০ এক (৩০ পিস) বক্সের দাম আগে ৪৮০ টাকা ছিল, যা এখন বেড়ে ৫২৫ টাকা হয়েছে। স্কয়ারের এনাফ্লেক্স ম্যাক্স ৫০০ মি.গ্রা. এর দাম ১৩০ টাকা থেকে বেড়ে ২১০ টাকা হয়েছে। একইভাবে স্কয়ারের এনাডল এস আর ১০০ মি.গ্রা. ১২০ টাকা থেকে বেড়ে ১৭০ টাকা, এরিস্টোফার্মার এক্সিম সিভি ৫০০ মি.গ্রা. ৫০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা, এসিআই কোম্পানির টেট্রাসল ৮০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা, ইনসেপ্টার এলিমেট প্লাস লোসন ১১০ টাকা থেকে ২০০ টাকা, স্কয়ারের রসুভা ১০ মি.গ্রা. ২০০ টাকা থেকে ২২০ টাকা, বেক্সিমকোর রসুটিন ১০ মি.গ্রা. প্রতি বক্সে ৬০ টাকা, স্কয়ারের এসিন্টা ম্যাক্স ২০০ এমএল বোতল ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা, এরিস্টোফার্মার এভোল্যাক সিরাপ ১০০ এমএল বোতল ১৬০ টাকা থেকে ২০০ টাকা এবং ২০০ এমএল বোতল ২৪০ টাকা থেকে ৩২০ টাকা হয়েছে।
এছাড়াও একমি কোম্পানির এন্টিবায়োটিক এজিন ৫০০ মিগ্রা প্রতি ট্যাবলেটে দাম বেড়েছে ২০ টাকা। ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির ওএমজি-৩০০ ক্যাপসুলের প্রতিটির মূল্য ৪০ টাকা বেড়েছে। একমি কোম্পানির গ্যাসের ওষুধ ডিডিআর ৩০ মি.গ্রা. প্রতি পাতায় বেড়েছে ১৫ টাকা। বেক্সিমকোর উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ এমডাকল ৫ মি.গ্রা. এর দাম ৭৩ টাকা থেকে বেড়ে ৮২ টাকা হয়েছে। নাপা সিরাপ ২০ টাকা থেকে ৩৫ টাকা, স্কয়ারের ইভিট ৪০০ মি.গ্রা. ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে।
ওষুধ বিক্রেতাদের মতে, গত সেপ্টেম্বর থেকে হঠাৎ করেই প্রায় অর্ধশত জীবন রক্ষাকারী ওষুধের দাম ১০ থেকে ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। অন্যান্য ওষুধের দামও ৩০ থেকে প্রায় ৯০-১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, বিশ্ববাজারে ওষুধের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ওষুধের দাম বেড়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর ডলারের দামের যে পরিবর্তন ঘটেছিল, সেটিও প্রায় দুই বছর আগের ঘটনা। বর্তমানে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ওষুধের দাম বাড়াতে হলে জাতীয় কমিটির মিটিং করা প্রয়োজন, কিন্তু এমন কোনো মিটিং হয়েছে বলে জানা যায়নি। এর অর্থ হলো, কোনো একটি চক্র ইচ্ছামতো ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে এবং সরকার এই চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।
ওষুধের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রতি বছর ৬০ লাখের বেশি মানুষ চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। ওষুধের দাম বৃদ্ধির ফলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। এছাড়াও নিম্নবিত্ত অনেকেই ওষুধ কিনতে পারবে না, ফলে তাদের অসুস্থতা দীর্ঘায়িত হবে। অনেকেই ওষুধ কিনতে গিয়ে খাবারের গুণগত মান কমিয়ে দেবে, যা পুষ্টিহীনতা বাড়াবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেবে।
স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদদের মতে, প্রতিযোগিতা বেশি থাকলে দাম কমার কথা। কিন্তু যেসব ওষুধের চাহিদা বেশি, সেগুলোর দামও বেড়েছে। উৎপাদন খরচ বাড়লেও তা ৫০ বা ৭০ শতাংশ বাড়েনি। তবে কিছু ওষুধের দাম তার চেয়েও বেশি বাড়ানো হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাব্বির হায়দার বলেন, জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলোর দাম ওষুধ প্রশাসন নির্ধারণ করে দেয়, সেগুলোর দাম মোটামুটি যৌক্তিক। তবে অন্যান্য ওষুধের দাম বেশি মনে হয়, কারণ সেগুলোর দাম নির্ধারণে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। অনেক কোম্পানি তাদের ওষুধের দাম ইচ্ছামতো বাড়িয়ে দেয়। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর গড় প্রফিট মার্জিন ৫০ শতাংশের বেশি, এমনকি কোনো ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত লাভ থাকে। চিকিৎসকদের বিভিন্ন উপহার দেয়ার মতো অনৈতিক ব্যয়ও ওষুধের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, যা ভোক্তাকেই পরিশোধ করতে হয়।
বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির মহাসচিব এম শফিউজ্জামান বলেন, নতুন ডিজি (ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক) আসার পর কোনো ওষুধের দাম বাড়েনি। বাজারে দাম বেড়ে থাকলে তা অন্য কোনো কারণে হয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মুখপাত্র ড. মো. আকতার হোসেনও দাম বৃদ্ধির বিষয়ে একই রকম বক্তব্য দিয়েছেন।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যকর ভূমিকার অভাব এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোর বেপরোয়া মুনাফার কারণে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। ওষুধের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আরও অসংখ্য মানুষ সর্বস্বান্ত হবে।












