
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী
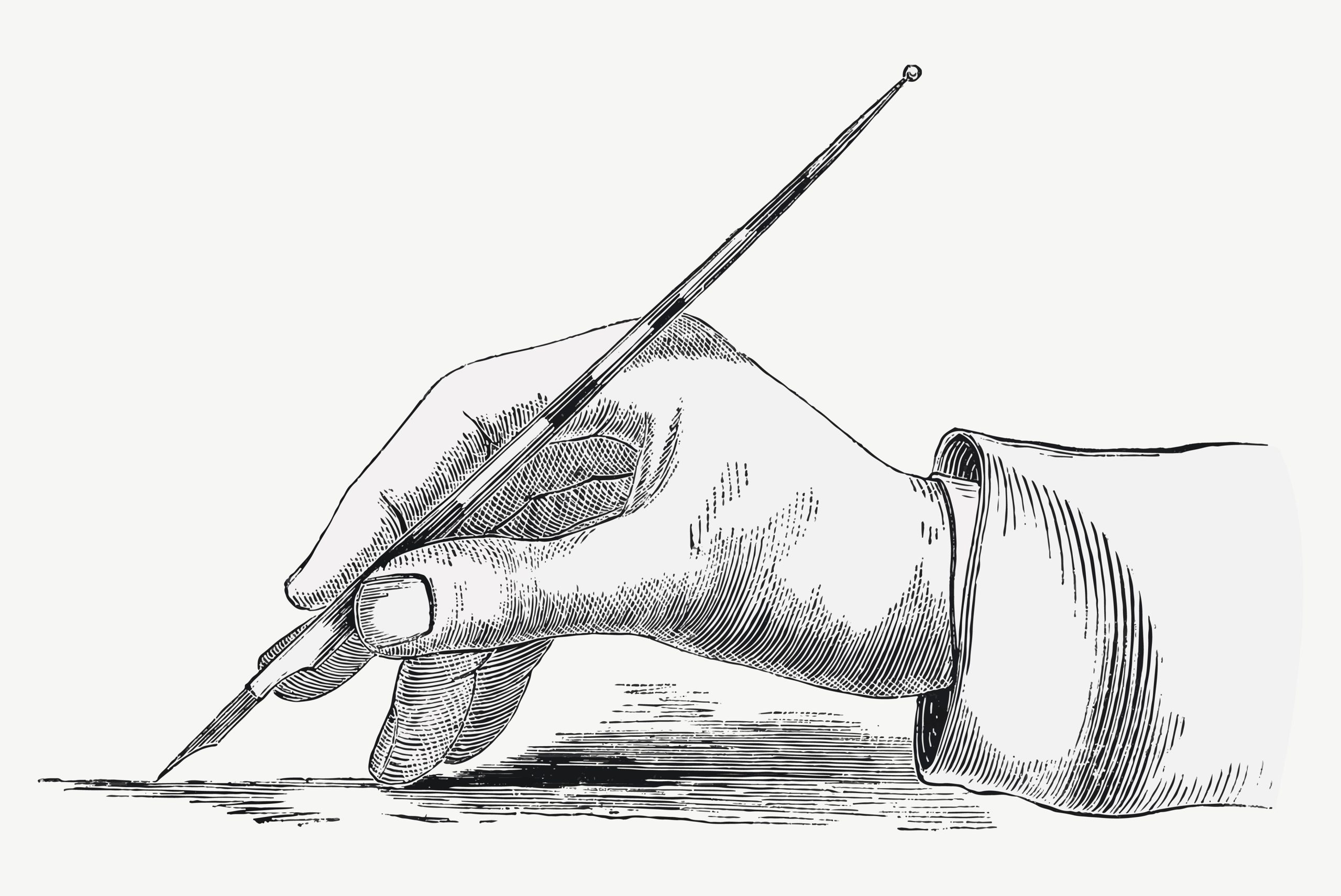
মানবসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ধারণা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। এক সময় রাষ্ট্রের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং রাজস্ব সংগ্রহ পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আরও ব্যাপক হয়েছে। এখন রাষ্ট্র শুধু শাসন নয়, জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাকেই প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে এমন এক রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখে। এই রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন— খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করে।
জাতিসংঘের ভাষায়—
“যে রাষ্ট্র নাগরিকদের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তাকেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়।”
অর্থনীতিবিদ পিগুর মতে,
“কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র যা তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে কাজ করে।”
অর্থনীতিবিদ পাউন্ড বলেন,
“যে রাষ্ট্র কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়, বরং মানবকল্যাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পৃক্ত করে— সেটিই প্রকৃত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।”
অতএব, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হলো এমন রাষ্ট্র যেখানে সরকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে, সামাজিক বৈষম্য দূর করে এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করে।
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ইতিহাস
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা খুব পুরনো। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল রাষ্ট্রকে জনগণের মঙ্গলসাধনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছিলেন। পরবর্তীতে অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকার কথা বলেন। তবে আধুনিক অর্থে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সূচনা ঘটে ১৯ শতকের শেষ দিকে, জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্কের সময়ে। তিনি কর্মীদের জন্য সামাজিক বীমা, পেনশন এবং স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করেন— যা আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করে।
বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (Great Depression) এবং ১৯৩০-এর দশকের সামাজিক বিপর্যয় রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল করে তোলে। এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ‘নিউ ডিল (New Deal) কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে ব্যাপক উদ্যোগ নেন। একইভাবে ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের বেভারিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যা আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নীতিগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলোতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র নিজে উদ্যোগী হয়।
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
১. জনকল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধতা
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সার্বিক কল্যাণ। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানসহ নানা উদ্যোগ নেয়।
২. অর্থনৈতিক কার্যক্রমে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ
এই রাষ্ট্রে সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্যবীমা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে।
৩. সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কেউ বৈষম্যের শিকার হয় না।
৪. সরকারি মালিকানার প্রসার
এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রসার ঘটে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, রেলওয়ে বা স্বাস্থ্যসেবা রাষ্ট্রের অধীনে থাকে।
৫. মিশ্র অর্থনীতি
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক নয়। এটি দু’য়ের মিশ্র রূপ— যেখানে সরকার ও বেসরকারি খাত উভয়ই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়।
৬. অশিক্ষা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ
রাষ্ট্র অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শিক্ষাকে সবার জন্য সহজলভ্য করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৭. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষা
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যেমন— ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও বিচার পাওয়ার অধিকার সর্বাগ্রে গুরুত্ব পায়।
৮. উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
টি. এইচ. মার্শালের মতে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ধনীদের আধিপত্য বা শ্রমিকদের একনায়কতন্ত্র নয়— বরং এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি ব্যবস্থা, যেখানে ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ অগ্রগণ্য।
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী
১. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও কর সংগ্রহ
রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে সমাজে স্থিতিশীলতা আনে। পাশাপাশি জনগণের কাছ থেকে কর সংগ্রহের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব অর্জন করে, যা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়।
২. জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে। হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ও মাতৃসেবা নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও বেকার নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু থাকে।
৩. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন
এই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করে। একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও বাজার স্থিতিশীলতা বজায় রাখাও এর কাজের অন্তর্ভুক্ত।
৪. অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ
রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থা গণমুখী করে তোলে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প, ব্যাংক ও বীমা খাতে সুযোগ সৃষ্টি করে।
৫. সবার অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত থাকে। বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নারী-পুরুষ সমতা ও বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।
৬. জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
রাষ্ট্র নিজেকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখে।
৭. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও শিল্পোন্নয়ন
রাষ্ট্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা করে।
৮. সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিনোদন
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মানসিক বিকাশেও ভূমিকা রাখে। সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও ক্রীড়া চর্চায় রাষ্ট্র উৎসাহ দেয় এবং নাগরিকদের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে।
৯. ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা
জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করে। কেউ যেন অন্যায়ভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুরক্ষা দেয়।
সংগৃহীত । সিএনআই / ২৫
কপিরাইট © ২০২৪ || সেন্ট্রাল নিউজ ইনভেস্টিগেশন